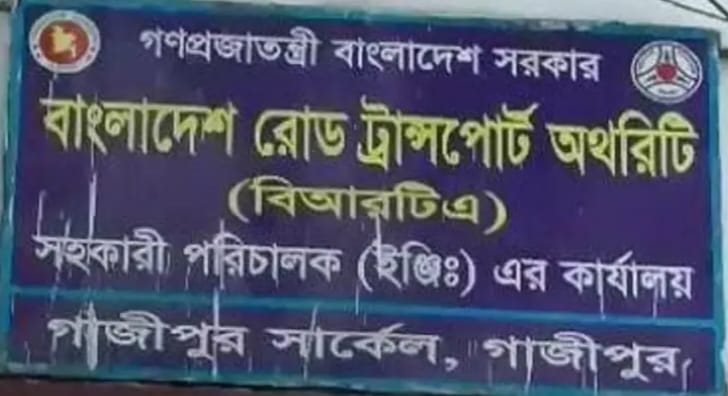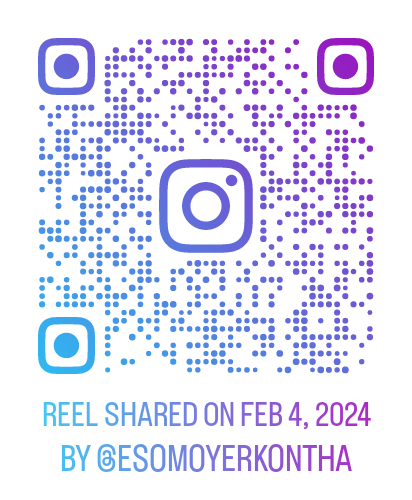যুগে যুগে চাকমা নেতৃত্বে স্বার্থপরতা এবং অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম

- আপডেট টাইম : ০৭:০৯:২৪ পূর্বাহ্ন, মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর ২০১৭
- / ৭১৭ ১৫০.০০০ বার পাঠক
১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উপজাতি নেতৃত্বের সাথে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল তার ফলস্বরূপ এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা কাঙ্ক্ষিত ছিল। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে শান্তিচুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়নের করেছে এবং অবশিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ভূমিবণ্টনসহ অন্যান্য কিছু মৌলিক বিষয়ে বিভিন্ন দল ও জনগোষ্ঠীর মতামতে ভিন্নতা শান্তিচুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করেছে।
ইতোমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি আঞ্চলিক নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তির কারণেও চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পিসিজেএসএস ছাড়াও অন্য আরও দুইটি আঞ্চলিক উপজাতি দল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে একটি দল ইউপিডিএফ শান্তিচুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে স্বায়ত্বশাসন দাবি করছে। অন্যদিকে আঞ্চলিক অপর দল জেএসএস (সংস্কার), জেএসএস (মূল) দলের সাথে নেতৃত্বের সংঘাতে জড়িয়ে পৃথক অবস্থানে রয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ফিরে আসার কথা থাকলেও সেই অনুযায়ী আশানুরূপ শান্তি ফিরে আসেনি। আঞ্চলিক উপজাতি তিনটি দলই পৃথক পৃথক সশস্ত্র গ্রুপ পরিচালনা করে।
তিনটি দলই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে নিয়মিত চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক উপজাতি দলসমূহের সশস্ত্র সংগঠনসমূহ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ উপজাতি-বাঙালি অধিবাসীগণ উল্লেখিত তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজীতে অতীষ্ঠ। সশস্ত্র সংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্যের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে উঠছে না কোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমূলক স্থাপনা।
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানে এই অশান্ত হয়ে ওঠা, শান্তিচুক্তির পরেও সাধারণ উপজাতি, বাঙালিদের নিরাপত্তাহীনতা এসব কিছুর জন্যই কিছু কিছু উপজাতি নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা গ্রহণের লিপ্সাই দায়ী।
ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আঞ্চলিক উপজাতি দলসমূহের নেতৃত্বে সব সময় চাকমা সম্প্রদায়ই সুদৃঢ় অবস্থানে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। বর্তমানে অশান্ত এই পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আঞ্চলিক দল এবং এর সশস্ত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মূলত চাকমারাই আছে।
একই সাথে আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শান্তিচুক্তির ফলে গড়ে ওঠা সংস্থাসমূহ যেমন- আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ ইত্যাদিতে চাকমা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। একই সাথে বিদেশি সংস্থাসমূহের শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে চাকমা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব প্রাপ্ত রয়েছে।
তাই সার্বিকভাবে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধানত ১৩ থেকে ১৪টি উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও সর্বক্ষেত্রেই চাকমা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই নেতৃত্বের অবস্থানে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চাকমা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব কতটুকু সাধারণ উপজাতিদের কল্যাণে কাজ করছে এবং চাকমা ব্যতিত অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিবাসীবৃন্দই বা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে।
পার্বত্য অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ এবং চাকমা সম্প্রদায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চাকমা নেতৃত্বের মধ্যে এক প্রকার স্বার্থপরতা, ক্ষমতার প্রতি লোভ এবং যেকোন প্রকারে শীর্ষস্থান দখলের প্রবণতা কাজ করেছে। চাকমা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সবসময় ‚নিজ এবং ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে দেখা গেছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায়ের জমিদারদের মধ্যে স্বীকৃত প্রথম জমিদার কালিন্দি রায়ের সিপাহী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, ইংরেজদের তুষ্ট করার প্রবণতা, ইংরেজ কর্তৃক দেশ বিভাগের সময় সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের ভারতের সাথে সংযুক্তির ইচ্ছে থাকলেও নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নলিনাক্ষ রায়ের পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তিতে স্বস্তি, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানকে সমর্থন ও সহযোগিতা, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এম এন লারমা কর্তৃক সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠন, দেবাশীষ রায়ের দেশবিরোধী প্রচারণার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্বার্থন্বেষী মহলের সহায়তায় নতুন উদ্ভাবিত ‘আদিবাসী’ দাবি ইত্যাদি, এসব কিছুই চাকমা সম্প্রদায়ের কোন কোন গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ফুটে ওঠে।
সার্বিক বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আসুন চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেয়া যাক। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, চাকমারা মঙ্গলীয় জাতির একটি শাখা, বর্তমান মায়ানমারের আরাকানে বসবাসকারী ডাইংনেট জাতি গোষ্ঠীকে চাকমাদের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়। চাকমারা প্রধানত থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, চাকমাদের ভাষার নাম চাকমা (চাংমা)। চাকমারা ৪৬টি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পূর্বে এ জাতি হরি ধর্মের অনুসারী হলেও পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। চাকমা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘শক্তিমান’ থেকে আগত। বর্মী রাজত্বের শুরুর দিকে বর্মী রাজারা ‘চাকমা’ শব্দটি প্রচলন করেন।
তখনকার সময় বর্মী রাজারা চাকমাদের রাজার পরামর্শক, মন্ত্রী এবং পালি ভাষার বৌদ্ধ ধর্মের পাঠ অনুবাদকের কাজে নিয়োগ করতেন। রাজা কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত হওয়ায় বর্মী রাজ পরিবারে চাকমারা বেশ প্রভাবশালী ছিলো। তবে চাকমাদের চতুরতা ও স্বার্থপরতা বর্মীদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। বার্মায় প্রচলিত চাকমাদের নাম সংক্ষেপ ‘সাক’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘শক্তিমানের’ বিকৃত রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে এই জনগোষ্ঠীর নাম ‘সাকমা’ এবং কালক্রমে ‘চাকমা’ নামেই পরিচিতি লাভ করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চাকমা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবেই বিভিন্ন মহলের নেতিবাচক অনুভূতি ছিল।
পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ চাকমাই আরাকান অঞ্চল থেকে শরণার্থী হিসেবে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এসেছিল। চাকমাদের তথাকথিত রাজবংশের শুরুটা ছিল কালিন্দি রায়ের মৃত্যুর পর থেকে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কালিন্দি রায় ও ধরম বক্স খাঁ’র কন্যা মেনকা এবং তার স্বামী গোপীনাথ দেওয়ান চাকমার সন্তান হরিশ্চন্দ্র রায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের জমিদারির দায়িত্ব পাবার পর, ‘এই অঞ্চলটি চাকমাদের’ এরূপভাবে প্রচার পেতে শুরু করে।
মোঘল জমিদার ধরম বক্স খাঁর মৃত্যুর পর তার প্রথম স্ত্রী কালিন্দি রায় (যিনি চাকমা সম্প্রদায় থেকে জমিদার পরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলেন) ব্রিটিশদের আনুকূল্যে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা লাভের পূর্বে চাকমাদের জন্য পৃথক কোন জমিদারি ছিল না। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে চাকমা সম্প্রদায় আরাকানিদের নিকট থেকে বিতাড়িত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে বান্দরবানের আলীকদমে অবস্থান নেয়, তবে চাকমাদের পূর্বে আলীকদমে মোঘলদেরও অবস্থান ছিল। বিভিন্ন সময় উত্থান পতনের পর আলীকদম থেকে মোঘল জনগোষ্ঠীর জমিদারগণ ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থান নেন।
আর এখানে প্রথম জামিদারি স্থাপন করেন শেরমস্ত খাঁ (১৭৩৭-১৭৫৩ খ্রি.)। এরপর যথাক্রমে রাজা শুকদেব (১৭৫৩-১৭৫৮ খ্রি.), রাজা শের জব্বার খাঁ (১৭৫৮-১৭৬৫ খ্রি.), রাজা শের দৌলত খাঁ (১৭৬৫-১৭৮২ খ্রি.), রাজা জানবক্স খাঁ (১৭৮২-১৮০০ খ্রি.), রাজা তব্বার খাঁ (১৮০০-১৮০১ খ্রি.), রাজা জব্বর খাঁ (১৮০১-১৮১২ খ্রি.), রাজা ধরম বক্স খাঁ (১৮১২-১৮৩২ খ্রি.) এবং কালিন্দি রায় (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে জমিদারি পরিচালনা করেন। কিন্তু এই জমিদার পরিবারের বিপত্তি শুরু হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজা জব্বর খাঁ তার উত্তরাধিকার হিসেবে কোন পুত্র না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজা জব্বর খাঁর মৃত্যুর ১৮ মাস পর তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তানের (ধরম বক্স খাঁ) জম্ম হলে ঐ সন্তানকে জমিদারের উত্তরাধিকারী হিসেবে কেউ মেনে নিতে চায়নি। ব্রিটিশরা এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে।
তারা জমিদার পরিবারের বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসলিম এবং মোঘলদের কোণঠাসা করতেই বিতর্কিত শিশু ধরম বক্স খাঁ’র পক্ষ নেয় এবং তাদের সহযোগিতায় ধরম বক্স খাঁ জমিদার হিসেবে ঐ সময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে রাজা ধরম বক্স খাঁ মৃত্যুবরণ করায় আদালতের রায়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার মোঘল বংশাজাত সুখলাল খাঁকে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু ধরম বক্স খাঁ’র স্ত্রী কালিন্দি রায় (চাকমা সম্প্রদায়ের মেয়ে, ধরম বক্স খাঁ’র স্ত্রী) বিষয়টি আদালতে আপিল করলে দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে তার অনুকূলে রায় পান। তারপর থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালিন্দি রায় জমিদারী পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করেন। কালিন্দি রায়ের মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্র জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমান চাকমা সম্প্রদায়ের তথাকথিত রাজাদের রাজত্ব হরিশ্চন্দ্র থেকেই শুরু হয়েছিল।
এখানে আরো একটি বিয়য় বলে রাখা ভালো। ১৮৫৭ সালে হরিশ্চন্দ্র তৎকালীন জমিদার কালিন্দির নির্দেশে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সহায়তা করার উপহার স্বরূপ রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে হরিশ্চন্দ্র জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণের পর রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর থেকে তার জমিদারী রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করেন। রাঙ্গামাটিতে চাকমাদের জমিদারি স্থানান্তরের পর যথাক্রমে হরিশ্চন্দ্র রায় (১৮৭৩-১৮৮৫ খ্রি.), ভুবন মোহন রায় (১৮৮৬-১৯৩৩ খ্রি.), রাজা নলিনাক্ষ রায় (১৯৩৪-১৯৫১ খ্রি.), রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৫২-১৯৭১ খ্রি.), রাজা কুমার সুমিত রায় (১৯৭২-১৯৭৭ খ্রি.) এবং রাজা দেবাশীষ রায় (১৯৭৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত) চাকমা সম্প্রদায়ের রাজা হিসাবে কর্তব্য পালন করছেন। এখানে উল্লেখ্য, চাকমা সম্প্রদায়ের জমিদারদেররায় ‘বাহাদুর’ উপাধি থাকলেও তারা ‘রাজা’ ছিল না।
১৯৩৯ সালের ৮ জুন ইংরেজ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের জন্মদিবস উপলক্ষে সম্রাট জয়ন্তীতে তৎকালীন চাকমা জমিদার নলিনাক্ষ রায়কে ‘রাজা’ উপাধি প্রদান করা হয়। তার পর থেকে নলিনাক্ষ রায় নিজে এবং তার উত্তরাধিকারীগণ তাদের নামের শুরুতে ‘রাজা’ উপাধি ব্যবহার করছেন। ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের দূরবস্থার সাথে সাথে প্রভাবশালী হিন্দুদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। চাকমা সম্প্রদায়ের মেয়ে বিচক্ষণ জমিদার কালিন্দি রায়ও এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন বিধায় তিনি ইংরেজদের সহায়তায় জমিদারির দখল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক সিপাহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেন।
এ বিষয়ে মোহাম্মদ ওয়াজিউল্লাহ তার ‘আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম’, ১৯৬৭, পৃ.-১০৩-এ লিখেছেন, ‘কালিন্দির পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে চাকমাদের সাথে ব্রিটিশ কোম্পানির তেমন কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। বিচক্ষণ কালিন্দি রায় আনুগত্য লাভের আশায় ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। এমনকি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহকালে বিদ্রোহী সৈনিকরা পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করলে, কালিন্দি রায় তাদেরকে ধৃত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সৈনিকদের বিরুদ্ধে এহেন দায়িত্ব পালনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে কালিন্দি রায়কে কর্ণফুলী নদীর বার্ষিক জলকর (১১৪৩ টাকা) মওকুফ করে দেয়।’ অর্থাৎ কালিন্দি রায়ের হাত ধরে যে চাকমা রাজত্বের ইতিহাস শুরু সেই ইতিহাসে রয়েছে কালিন্দির স্বামী ধরম বক্সের বিতর্কিত পিতৃ পরিচয় এবং পরবর্তীতে নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সিপাহী বিদ্রোহে স্বাধীনতাকামীদের সাথে বেঈমানির ইতিহাস।
১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর রাঙ্গামাটিতে চাকমাদের অন্য একজন রাজনৈতিক নেতা স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারিত হচ্ছে এই হিসেবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের সাথে যুক্ত হবে এই আশায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ আলোচিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। যদিও তৎকালীন ইংরেজ জেলা প্রশাসক কর্নেল জি. এল. হাইড নিজেও উক্ত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পতাকায় স্যালুট করেন তথাপি বাউন্ডারি কমিশনের প্রধান স্যার সিরিল রেডক্লিফ এর নেতৃত্বাধীন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং অবস্থানগত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এলাকাটি পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্তটি অনেককে অবাক করলেও, তৎকালীন চাকমা রাজা নালিনাক্ষ রায় খুশিই হয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, ভারতের কংগ্রেস নীতি অনুযায়ী তারা স্বাধীন ভারতে কোন ধরনের স্থানীয় রাজা-রাজ কুমার বা রাজকীয় ক্ষুদ্র রাজ্য মেনে নেবে না। চাকমা রাজার পক্ষে ভারতে যোগ দিয়ে রাজত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হতো।
রাজা নলিনাক্ষের মৃত্যুর পর তার পুত্র ত্রিদিব রায় যখন ১৯৫১ সালে রাজা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করা শুরু করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এমপি। কাপ্তাই হাইড্রো প্রজেক্টের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের সাথে প্রথম দিকে মতবিরোধ থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রলোভনে তিনি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা শুরু করেন। রাজা ত্রিদিব রায় মনে করেছিলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করবে।
তাই পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। লন্ডনভিত্তিক ভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রিয়জিত দেব সরকার রচিত তার বই ‘দ্য লাস্ট রাজা অর ওয়েষ্ট পাকিস্তান’ বইটির তথ্য অনুযায়ী, ত্রিদিব রায়ের সিদ্ধান্ত ছিল আত্মস্বার্থ কেন্দ্রিক। নিজের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতেই ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়েছেন। উনি চাইছিলেন তার রাজত্ব এবং রাজ পরিবারের শাসন যেন বজায় থাকে। যদিও অনেক সাধারণ চাকমা তার নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া না দিয়ে ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে না দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। চাকমা রাজা হিসেবে তার প্রভাবাধীন হেডম্যান-কারবারীদের ব্যবহার করে চাকমা যুবকদের দলে দলে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করেন। তাদের ট্রেনিং এবং অস্ত্র দিয়ে লেলিয়ে দেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানের পরাজয় অনুধাবন করতে পেরে ত্রিদিব রায় ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় মিয়ানমার হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যান।
বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বের হওয়া হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র’ (সশস্ত্র সংগ্রাম-১) নবম খণ্ডের (জুন, ২০০৯) ৯৩ পৃষ্ঠায় মে.জে. মীর শওকত আলী (বীর উত্তম) লিখেছেন, ‘চাকমা উপজাতিদের হয়ত আমরা সাহায্য পেতাম। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরোধিতার জন্য তারা আমাদের বিপক্ষে চলে যায়।’
অন্যদিকে ১৯৭১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক (বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা) এইচটি ইমাম তার বই ‘বাংলাদেশ সরকার-১৯৭১’-এর (মার্চ, ২০০৪) ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় প্রথম থেকেই নির্লিপ্ত এবং গোপনে পাকিস্তানীদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন।’ বাংলাদেশ এবং বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাব ও কার্যক্রমের পুরস্কার স্বরূপ ‘পাকিস্তানের জাতীয় বীর’ খেতাব এবং আজীবন মন্ত্রিত্ব নিয়ে তিনি পাকিস্তানেই বসবাস করেছেন।
অপরদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের রেখে যাওয়া রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) গড়ে তোলেন সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। গত তিন যুগের বেশি সময় ধরে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে হাজার হাজার নিরীহ পাহাড়ি বাঙালি জনগণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। এদেরই উত্তরসূরিদের হাতে এখনো অব্যাহতভাবে চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং খুনের শিকার হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অসহায় মানুষগুলো।
২০০৩ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী মূলক বই The Departed Melody-তে ত্রিদিব রায় নিজেই রাজাকার হিসেবে তার কর্মকাণ্ড বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এসব অপকর্মের কারণে তিনি অনুতপ্ত তো ননই বরং গর্ব প্রকাশ করেছেন তার বইয়ে। একই সাথে তিনি মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ব্যঙ্গ করার পাশাপাশি পাকিস্তানী হানাদারদের প্রসংশা করেছেন।
১৯৭১ সালের নভেম্বরে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানী সৈন্যদের সহায়তায় মায়ানমার হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তান সরকার তাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে ঐ বছরই থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে প্রেরণ করে। জাতিসংঘের ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত জেনারেল এসেম্বলিতে বাংলাদেশের সদস্য পদ প্রদানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে পাকিস্তান সরকার-এর বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং করার জন্য ত্রিদিব রায়কে প্রধান করে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ত্রিদিব রায়ের লবিংয়ের কারণে চীন ভেটো প্রয়োগ করায় ঐ বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে ব্যর্থ হয়।
তার এই সফলতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার মন্ত্রিসভা জাতিসংঘ ফেরত ত্রিদিব রায়কে ‘জাতীয় বীর’ খেতাব দিয়ে লাল গালিচা সংবর্ধনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ত্রিদিব রায় ধারাবাহিকভাবে পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সভা-সেমিনারে বক্তব্য দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, বই লিখে বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। গত ২০০০ সালের ৪ অক্টোবর পাকিস্তানি ইংরেজী দৈনিক ডন পত্রিকায় ‘চিটাগং হিল ট্র্যাক্ট: লেট জাস্টিস বি ডান’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ The Departed Melody-তে সরাসরি বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতাবিরোধী বক্তব্য রেখেছেন।
ত্রিদিব রায় পাকিস্তান সরকারের কাছে এতটাই অনুগত ছিলেন যে, তাকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ফেডারেল মন্ত্রী, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত পর্যটন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ১৯৮১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার ৫টি দেশের রাষ্ট্রদূত করে আর্জেন্টিনায় প্রেরণ, ১৯৯৫ সালের মে মাস থেকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় এ্যাম্বাসেডর এ্যাট লার্জ হিসেবে নিয়োগ, ২ এপ্রিল ২০০৩ থেকে পাকিস্তানের দপ্তর বিহীন ফেডারেল মন্ত্রী হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজা ত্রিদিব রায়ের উত্তরসূরি তার সন্তান তথা বর্তমান চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এর ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বলে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।
‘আদিবাসী’ ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিরোধী বক্তব্য এবং অব্যাহত অপপ্রচার তারই সাক্ষ্য বহন করে। চাকমা রাজপরিবারের প্রধানদের ধারাবাহিক এসব কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তারা সব সময়ই এদেশ এবং এদেশের মুক্তিকামী মানুষের আবেগ ও প্রত্যাশার বিরোধী ছিল এবং এখনো তাদের মধ্যে এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাসকে স্বার্থপরতার ইতিহাস বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।
দেবাশীষ রায় ১৯৯৮ সালে ‘টংগ্যা’ নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ করে বাঙালি বিদ্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এনজিওগুলোর সমন্বয়ে হিল ট্র্যাক্ট এনজিও ফোরাম (এইচটিএনএফ) নামের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। এর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি নিজেই। সংগঠনটির বাঙালি বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড এবং পাহাড়ে জাতিগত বৈষম্য তৈরিতে ভূমিকা রাখার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক উক্ত এনজিওর কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে এইচটিএনএফ এর আদলে প্রতিষ্ঠা করা হয় এইচটিএনএন নামের আরো একটি সংগঠন।
ব্রিটিশ আমল থেকেই সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে বাধার সন্মুখীন হয়ে এসেছে। প্রথম দিকে ব্রিটিশরা তাদের শাসন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে কিছুসংখ্যক পাহাড়িকে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলে চাকমা রাজপরিবার থেকে বাধা দেয়া হয়। ব্রিটিশরা ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান চালু করেও এই পাহাড়ি নেতাদের আন্দোলনের কারণেই তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।
এখানে উল্লেখ্য রাঙ্গামাটি হাই স্কুলও সাধারণ পাহাড়িদের শিক্ষিত করার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, বরং বর্তমান চাকমা সার্কেল চীফের পূর্ব পুরুষ ভূবন মোহন রায়কে শিক্ষিত করার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯০ সালে গড়ে তোলা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটি কলেজ। কিন্তু এটি স্থাপনও সহজ কাজ ছিল না। কারণ তৎকালীন চাকমা সার্কেল চীফ ত্রিদিব রায় রাঙ্গামাটিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হননি বরং এটি যাতে কোনভাবেই বাস্তবায়িত হতে না পারে সে চেষ্টাও করেছিলেন। এর জন্য তিনি প্রথমে ঢাকার রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এস এম হাসানের কাছে এবং পরবর্তীতে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার করিম ইকবালের কাছে চিঠি লিখে রাঙ্গামাটিতে কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সিদ্দিকুর রহমানের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
চাকমা রাজপরিবার কর্তৃক সাধারণ পাহাড়িদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় সৃষ্টির আরো অনেক নির্মম ইতিহাস পাওয়া যাবে অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত শরদিন্দু শেখর চাকমার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন (প্রথম খন্ড)’ এর বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে চাকমা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন উপজাতি আঞ্চলিক দলগুলোর প্রবল বাঁধার মুখে পড়ে। পরবর্তীতে সরকার উপজাতি নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করতে সমর্থ হয়।
সার্বিক বিষয় বিশ্লেষনে নিঃসন্দেহে বলা যায় তৎকালীন চাকমা নেতৃত্ব ঐতিহাসিকভাবে সবসময় ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা ব্রিটিশ সরকারের সময় ব্রিটিশদের অনুগত ছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের গ্রেফতারে সরাসরি সহায়তা করেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি যখন ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের অধীনস্ত হওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেছিল, তখন তৎকালীন চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় অন্যান্য উপজাতিদের মতামতের আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা না নিয়ে, ব্রিটিশদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির বিষয়ে খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তান সরকারের অনুগত ছিলেন।
১৯৫৮ সালে যখন কাপ্তাই বাধ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন চাকমা নেতৃবৃন্দ তাদের জাতিগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা না করে পাকিস্তান সরকারের অনুগত হিসেবে অবস্থান নিয়েছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন পশ্চিম পাকিস্তানের একপেশে আচরণের কারণে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ ছিল তখনও চাকমা নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অনুগত হিসেবে অবস্থান নিয়েছিলো। তৎকালীন চাকমা সার্কেল প্রধান স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করার সময় যখন অনুভব করলেন পাকিস্তানের পরাজয় সুনিশ্চিত তখন তিনি পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এখানে যদি তিনি তার মাতাদর্শের বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন তা হলে স্বপরিবারে পালিয়ে যেতে পারতেন, তা না করে বাংলাদেশে তার সম্প্রদায়ের অবস্থান ধরে রাখা এবং একই সাথে নিজে পাকিস্তানে অবস্থান করে বাংলাদেশবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যখন একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন চাকমাদের আরেক নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বঙ্গবন্ধুর স্নেহসুলভ একটি উক্তির (তোরা সব বাঙালি হয়ে যা) অজুহাতে শান্তিবাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। চাকমা নেতৃত্ব সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল শুধুমাত্র তাদের প্রতি করা বঙ্গবন্ধুর সেই সরল উক্তিকে তারা অহেতুক অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। শান্তিবাহিনী সাথে সংঘর্ষে অসংখ্য পাহাড়ী, বাঙালি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়েছেন।
চাকমা নেতৃত্বের একাংশের স্বার্থপরতা এবং একপেশে নীতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপজাতি অধিবাসীগণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। চাকমা নেতৃত্ব কখনও অন্য জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিকাশ সহ্য করে না। চাকমা ব্যতিত অন্য জাতিগোষ্ঠির মধ্যেও যে মেধা রয়েছে তার অনেক উদাহরণ বর্তমান সমাজে রয়েছে। সামাজিকভাবে সহায়তার অভাব এবং পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার প্রবৃদ্ধিতে বাধা সত্ত্বেও চাকমা ব্যতিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপজাতিগণ নিজস্ব মেধা ও শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।
খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে, গুইমারাতে মারমা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এবং বান্দরবানে চাকমা ব্যতিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং অধিবাসীগণও উল্লেখযোগ্যভাবে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে চাকমারা অযাচিতভাবে প্রভাব বিস্তার না করলে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির আরো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। চাকমাদের সৃষ্ট অশান্ত এই পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা স্বাভাবিক হলে অপার সম্ভাবনাময় এই অঞ্চলে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটত।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন প্রকার কল-কারখানা, পর্যটনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটত। সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক হতো। ঐতিহাসিকভাবে চাকমা নেতৃত্বের স্বার্থপরতাজনিত এই বিতর্কিত ভূমিকা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থবিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে।
চাকমা সম্প্রদায়ের ৪৬ ধরনের গোত্রের মধ্যে অধিকাংশ গোত্র সাধারণ উপজাতি ও বাঙালিদের সাথে মিলে মিশে এক সাথে কাজ করতে চায়। ঐতিহাসিকভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের বিতর্কিত প্রশ্নবৃদ্ধ ভূমিকা সাধারণ পাহাড়ী, বাঙালিদের জনজীবন অতিষ্ঠ করাসহ দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বার্থান্বেষী গুটি কয়েক চাকমা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আচরণ এবং কার্যক্রমের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসছে না।
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনরুদ্ধারে এবং উক্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক শিল্পায়ন প্রয়োজন। যুগে যুগে চাকমা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের স্বার্থপরতার জন্য উচ্চবিত্তদের সন্তানগণ শিক্ষার আলো পেলেও, সাধারণ পাহাড়ীদের সন্তানগণ শিক্ষাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতি/গোষ্ঠী নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জনগণের আগামী প্রজম্মকে উন্নত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চাকমা সম্প্রদায়ের চিহ্নিত কিছু নেতৃবৃন্দের নিজ জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে সহমত প্রকাশ না করে, নিজ দেশ বাংলাদেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে আরো উন্নত গর্বিত বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, এই প্রত্যাশা সকলের।